
প্রকাশিত হয়েছে :
সংশোধিত :

পুরান ঢাকার পাটুয়াটুলিতে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের পাশে খেয়াল করলেই চোখে পড়বে লালবর্ণের একটি দালান। একতলা ভবন, তবে উচ্চতায় দোতলার সমান। ব্রিটিশ স্থাপত্যশৈলিতে নির্মিত ভবনটি প্রকৃতপক্ষে একটি উপাসনালয়। রাজা রামমোহন রায়ের প্রবর্তিত ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যদের উপাসনার জন্য নির্মিত হয়েছিলো এটি।
সেটি ১৮৬৬ সালের কথা। দীননাথ সেন ঢাকায় ব্রাহ্মদের নিজস্ব উপাসনালয় নির্মাণের প্রস্তাব করেন। সে বছরের ২৫ আগস্ট এ বিষয়ে ৯ সদস্যের কমিটি গঠিত হয়। তখন আরমানিটোলার ব্রাহ্মসমাজ গৃহে তারা প্রার্থনার জন্য সমবেত হতেন। বাড়িটি ছিলো একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের। যদিও এ নিয়ে মতান্তর আছে। ভিন্ন মতানুসারে কলতাবাজারের জমিদারেরা (বসাক পরিবার) সেই জমি ও বাড়ির মালিক ছিলেন।
১৮৬৭ সালের এপ্রিলে অভয়কুমার দত্ত মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পরের বছরের ১০ সেপ্টেম্বর জমি নিবন্ধিত হয়। মন্দিরের নকশা করেন উমাকান্ত ঘোষ। রাসমাণিক্য সেন নির্মাণ কাজ পরিচালনা করেন। প্রায় দশ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৮৬৯ সালের ২২ আগস্ট নির্মাণ কাজ শেষ হয়৷ ধর্ম নির্বিশেষে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে সে বছরের ৫ ডিসেম্বর মন্দির উদ্বোধন করা হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন সম্পাদকের দায়িত্বে নিয়োজিত হন দীননাথ সেন। সে সময় প্রতি রবিবার প্রায় ৩০০ সদস্য এখানে প্রার্থনার জন্য সমবেত হতেন।
মন্দিরটি পূর্ব-পশ্চিমে আয়তাকার, চার ফুট উঁচু মঞ্চের ওপর নির্মিত। ছাদের সামনের অংশে নকশা করা চূড়োয় লেখা আছে 'ব্রাহ্মসমাজ।' পাঁচটি সিঁড়ি বেয়ে প্রবেশ করতে হয় মন্দিরে। মন্দিরের চারপাশে প্রশস্ত বারান্দা। তার ঠিক মাঝখানে বিশাল এক হলঘর। এটি ব্যবহৃত হয় মূল উপাসনালয় হিসেবে।
চারপাশের বারান্দা থেকে হলঘরে প্রবেশের জন্য আছে নির্দিষ্ট দূরত্বে ১৬ টি পথ। এই হলঘরে অবশ্য পূজা হয়না। হলঘরের উত্তর অংশের ঠিক মাঝখানে উঁচু বেদিতে বসে সম্পাদক ব্রাহ্ম মতবাদের কথা বলেন। বেদির সামনে বসে শিল্পীরা ব্রাহ্মমতের বিভিন্ন গান গেয়ে থাকেন। চারপাশের বেঞ্চে বসে শ্রোতারা তা শুনতে পারেন।
উল্লেখ্য, রাজা রামমোহন রায়ের হাতে প্রতিষ্ঠিত হলেও ব্রাহ্ম সমাজ গতি পায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়। এই মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্বে তিনিই ছিলেন। ব্রাহ্মমত নিরাকার ও একেশ্বরবাদী। উন্মুক্ত ছিলো ধর্ম নির্বিশেষে সবার জন্য। সে সময় যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে, নারী শিক্ষা ও বিধবা বিবাহের পক্ষে ব্রাহ্মসমাজ বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।
তবে বিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকে এই সমাজের অনুসারী কমতে থাকে। ঢাকায় সমাজের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আছেন রনবীর পাল। তিনি জানান, "ব্রাহ্মদের ভেতর দুটি ভাগ বা প্রকার আছে। জন্মসূত্রে ব্রাহ্ম ও অনানুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম। যারা এই মত সমর্থন করেন, কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেননি তারা দ্বিতীয় প্রকারের। তবে তারাও সমাজের সদস্য হতে পারেন। বর্তমানে ব্রাহ্ম আছেনা আমাদের দেশে ১০০ জনেরও কম। জন্মসূত্রে ব্রাহ্ম ১৫ জনের মতো হবেন।"

প্রতি রবিবার হয় সাপ্তাহিক প্রার্থনা ও গান
বাংলাদেশের প্রথম নারী বিবাহ রেজিস্টার কবিতা রানী দত্ত রায় ও চন্দনা পাল থাকেন এখানে। কবিতা রানীর স্বামী একজন ব্রাহ্ম। বিয়ের পর তিনিও এই সমাজের অংশ হয়েছেন। তিনি বলেন, “ব্রাহ্ম আর ব্রাহ্মণ -দুটো ভিন্ন জিনিস। তবে অনেকেই ব্রাহ্ম শব্দটি শুনে ব্রাহ্মণের মতো কিছু মনে করে। কিন্তু এই সমাজ আলাদা। এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো নিরাকার একেশ্বরবাদী আরাধনা ও সামাজিক সংস্কারের জায়গা থেকে।
ব্রাহ্ম সমাজের উদ্যোগে একসময় সামাজিক সংস্কারমূলক প্রচুর কাজ হয়েছে। তবে এখন কাজ হচ্ছে স্বল্পপরিসরে। রনবীর পাল জানান, "আমাদের ৭ সদস্যের কার্যনির্বাহী কমিটি আছে। ট্রাস্টি বোর্ডও আছে ৭ সদস্যের। মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য তারা করে থাকেন। আমরা শীতকালে বস্ত্র বিতরণ, অসুস্থদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা- ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করি।"
১৮৭১ সালে এখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি। ১৯১০ সালে এজন্য নির্মিত হয় আলাদা ভবন। তবে সেটির অবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় ২০১৫ সালে লাইব্রেরি সরিয়ে নেয়া হয়েছে মূল উপাসনা ভবনে। একসময় বই ও পুঁথির বিশাল সংগ্রহ থাকলেও ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের সময় ভবনটি ক্ষতিগ্রন্থ হয়। পাকিস্তানি হানাদেরদের অগ্নিসংযোগে লাইব্রেরির বহু বই পুড়ে যায়। এমনিতে এখন তেমন পাঠক নেই। বইপত্রে ধুলো জমে গেছে।
ব্রাহ্মসমাজের এই মন্দিরে পদধূলি পড়েছে অনেক রথি-মহারথিদের। ১৯২৬ সালে এখানে এসেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দীননাথ সেনের নাতবৌ সুচিত্রা সেনও স্বামী দিবানাথ সেনের সঙ্গে এখানে এসেছিলেন একবার।
খুব অল্প অনুসারী থাকলেও তাদের নিয়ে পরিপাটিভাবে চলছে ব্রাহ্মসমাজের কার্যক্রম। প্রতি রবিবার হয় প্রার্থনা। সম্পাদক রনবীর পাল বেদিতে বসে করেন আলোচনা। চলতে থাকে শিল্পীদের প্রার্থনাসঙ্গীত, যার ভেতর বড় একটি জায়গা নিয়ে রয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীত।
'সকাতরে ওই কাঁদিছে' কিংবা 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে' চলতে থাকে। চারপাশের বেঞ্চিতে বসে শ্রোতারা শুনতে থাকেন গান। প্রার্থনা শেষে নিভিয়ে দেয়া হয় মন্দিরের সব বাতি। কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ব্রাহ্মসমাজ আশ্রম।
mahmudnewaz939@gmail.com

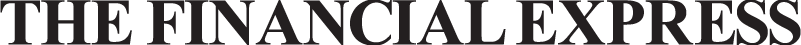
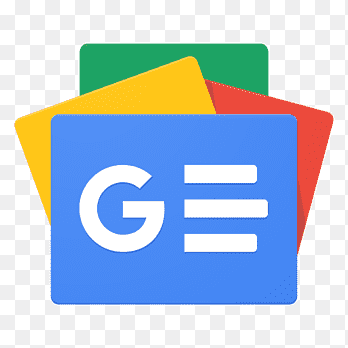 For all latest news, follow The Financial Express Google News channel.
For all latest news, follow The Financial Express Google News channel.