
প্রকাশিত হয়েছে :
সংশোধিত :

২১ ও ২২ নভেম্বর প্রায় ৩১ ঘণ্টার ব্যবধানে ঢাকা ও এর আশপাশে চারটি ভূমিকম্পের ঘটনা নগরবাসীকে বড় ধরনের ঝুঁকির কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। যদিও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে, বিশেষ করে ঢাকার আশেপাশে, খুব বড় মাত্রার ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল তুলনামূলকভাবে কম ছিল, তবুও ঐতিহাসিক ও ভূতাত্ত্বিক তথ্য বলছে ঢাকা একটি ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলের অত্যন্ত নিকটবর্তী এবং সর্বদা বড় বিপর্যয়ের ঝুঁকিতে রয়েছে।
২১ নভেম্বর সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে সৃষ্ট ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্পটি ছিল গত কয়েক দশকে ঢাকার কাছাকাছি হওয়া কম্পগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। এর উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদীর মাধবদীতে।
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের (বিএমডি) পরিচালক বলেন, "রিখটার স্কেলে ৫.৭ মাত্রার এই ভূমিকম্প মাঝারি হলেও এর উৎপত্তিস্থল (এপিসেন্টার) ঢাকার আগারগাঁও থেকে মাত্র ১৩ কিলোমিটার পূর্বে নরসিংদীতে হওয়ায় রাজধানীতে এর তীব্র ঝাঁকুনি অনুভূত হয়।"
এতে এখন পর্যন্ত তথ্য অনুযায়ী ১০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। আহত হন ৬ শতাধিক মানুষ। ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঢাকার এত কাছে এত বেশি মাত্রার ভূমিকম্প এর আগে কখনও অনুভূত হয়নি। তবে এই ভূমিকম্পের স্থায়িত্বকাল আর ৫-৭ সেকেন্ড বেশি হলেই ঢাকার অনেক ভবনই ধসে পড়ত এবং বড় ধরনের মানবিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা ছিল।
এ ধরনের ঘটনাকে অনেকে ভবিষ্যতে বড় ভূমিকম্পের 'ফোরশক' বা পূর্বাভাস হিসেবেও দেখছেন।
এরপর ২২ নভেম্বর সকাল ১০টা ৩৬ মিনিটে ৩ দশমিক ৩ মাত্রার আবার একইদিন সন্ধ্যা ৬টা ৪ মিনিটে কম্পন অনুভূত হয় যা উৎপত্তিস্থল নরসিংদী থেকে ১১ কিলোমিটার পশ্চিমে, এর মাত্রা ৪ দশমিক ৩। এর উৎপত্তি ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে।
ঢাকা তথা বাংলাদেশের ইতিহাসে বড় ভূমিকম্প পরিসংখ্যান ও তুলনা
ঢাকা ও এর আশপাশে ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল থাকার ঘটনা অতীতেও ঘটেছে, তবে মাত্রা ছিল কম। এর মধ্যে ২০১২ সালের ১৮ মার্চ ৪.৫ মাত্রা, ২০০৮ সালের ২৬ জুলাই ৪.৮ মাত্রা এবং ২০০১ সালের ১৯ ডিসেম্বর ৪.৫ মাত্রার ভূমিকম্প হয়। ওই ঘটনাগুলোতে বড় ধরনের হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে ২০১১ সালের ২৬ নভেম্বর চট্টগ্রামে ৬.২ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল।
ঐতিহাসিকভাবেও এ অঞ্চল বেশ কিছু বড় ভূমিকম্পের সাক্ষী।
প্রাচীন নথিভুক্ত ভূমিকম্প (১৫০০-এর দশক থেকে ১৮০০-এর দশক)
১৫৪৮ সালের ভূমিকম্প
বর্তমান বাংলাদেশের ভূখণ্ডে নথিভুক্ত প্রথম প্রধান ভূমিকম্প এটি। এই ভূমিকম্পে এখনকার চট্টগ্রাম ও সিলেটের কিছু অংশে ফাটল সৃষ্টি হয়। ঐতিহাসিক বিবরণ অনুযায়ী, ফাটলগুলো থেকে দুর্গন্ধযুক্ত কাদা-জল নির্গত হয়েছিল। তবে কোনও হতাহতের খবর নথিবদ্ধ নেই।
১৬৪২ সালের ভূমিকম্প
একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প সিলেট জেলায় অনেক ভবন ও কাঠামোর ক্ষতি করে। পূর্বের ঘটনার মতো এক্ষেত্রেও কোনো মানব হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
১৭৬২ সালের মহাবিপর্যয় (এপ্রিল)
এই অঞ্চলের ইতিহাসে অন্যতম মারাত্মক ভূমিকম্প এটি। 'ইস্টার্ন বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার চট্টগ্রাম' (১৯০৮) অনুসারে, চট্টগ্রাম জুড়ে মাটির ফাটল থেকে বিপুল পরিমাণ কাদা-জল বেরিয়ে আসে।
নথিতে 'পরদাবান' নামক একটি এলাকায় একটি বড় নদী শুকিয়ে যাওয়ার বিবরণও রয়েছে। 'বাকার চানাক' নামের একটি এলাকার প্রায় ২০০ জন মানুষ তাদের গৃহপালিত পশুসহ সাগরে তলিয়ে গিয়েছিল বলে জানা যায়। বলা হয়, এই ভূমিকম্পের ফলে সীতাকুণ্ড পাহাড়ের দুটি আগ্নেয়গিরির মতো মুখ তৈরি হয়েছিল।
১৮৬৫ সালের শীতকালীন ভূমিকম্প
'ইস্টার্ন বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার চট্টগ্রাম' (১৯১২) এ এই ভূমিকম্পের বিবরণ পাওয়া যায়। সীতাকুণ্ডের একটি পাহাড়ে ফাটল থেকে বালি ও কাদা নির্গত হয়েছিল। আর কোনও গুরুতর ক্ষতির কথা জানা যায় না।
১৮৮৫ সালের বেঙ্গল ভূমিকম্প (প্রায় ৭ মাত্রার)
১৮৮৫ সালে মানিকগঞ্জে আঘাত হানা এই ভূমিকম্পটি 'বেঙ্গল ভূমিকম্প' নামে পরিচিত। এর সম্ভাব্য উপকেন্দ্র ছিল সাটুরিয়ার কোদালিয়ায়, যা ঢাকা থেকে প্রায় ১৭০ কিলোমিটার দূরে।
এই কম্পনটি বিহার, সিকিম, মণিপুর এবং মায়ানমার পর্যন্ত অনুভূত হয়েছিল। ঢাকা, ময়মনসিংহ, শেরপুর, পাবনা এবং সিরাজগঞ্জের ভবন ও কাঠামোগুলোর ক্ষতি হয়েছিল, তবে সঠিক হতাহতের সংখ্যা জানা যায়নি।
১৮৯৭ সালের মহা-ভূমিকম্প (গ্রেট ইন্ডিয়ান আর্থকোয়েক)
এই অঞ্চলের সবচেয়ে বিধ্বংসী ভূমিকম্পগুলির মধ্যে একটি হলো ১৮৯৭ সালের ১২ জুনের ঘটনা, যা 'গ্রেট ইন্ডিয়ান আর্থকোয়েক' নামে পরিচিত। এর মাত্রা প্রায় ৮ অনুমান করা হয়।
সম্ভবত এর উপকেন্দ্র ছিল আসামের চেরাপুঞ্জির কাছে।
'ইস্টার্ন বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার চট্টগ্রাম' অনুসারে, এই ভূমিকম্প পুরো বাংলা জুড়ে, পূর্বের সাউথ লুসাই হিলস থেকে পশ্চিমের শাহাবাদ পর্যন্ত অনুভূত হয়েছিল। কম্পনের সময়কাল স্থানভেদে ছয় সেকেন্ড থেকে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত ছিল, যার মধ্যে চট্টগ্রামে দীর্ঘতম কম্পন অনুভূত হয়।
'বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার পাবনা' (১৯২৩) উল্লেখ করে, সিরাজগঞ্জের সাব-ডিভিশনাল অফিসের উপরের তলা, জেলখানা, ডাকঘর এবং আরও অনেক কাঠামো ধ্বংস হয়ে যায়। প্রায় সব ভবনেরই মারাত্মক ক্ষতি হয়। ঢাকায় প্রধান কাঠামোসমূহের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়। তৎকালীন অবিভক্ত বাংলায় ১,৫০০-এর বেশি মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয় এটি।
বিংশ শতাব্দীর ভূমিকম্পসমূহ (১৯১৮ সালের শ্রীমঙ্গল ভূমিকম্প)
প্রায় ৭.৬ মাত্রার এই ভূমিকম্পটি শ্রীমঙ্গলে আঘাত হানে। এটি মায়ানমার এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতেও অনুভূত হয়েছিল। শ্রীমঙ্গলের বহু ভবন ধসে পড়েছিল।
১৯৫০ সালের আসাম ভূমিকম্প
এই শতাব্দীর অন্যতম শক্তিশালী ভূমিকম্প (মাত্রা ৮.৭) ছিল ১৫ আগস্টের 'আসাম ভূমিকম্প'। এটি বাংলাদেশের বহু অংশে অনুভূত হলেও, দেশের অভ্যন্তরে বড় ধরনের কোনও ক্ষতি করেনি।
১৯৯৭ সালের চট্টগ্রাম ভূমিকম্প
১৯৯৭ সালের ২১ নভেম্বর ৬ মাত্রার একটি ভূমিকম্প চট্টগ্রামে আঘাত হানে, যার ফলে বিভিন্ন অবকাঠামোতে ফাটল দেখা দেয়।
১৯৯৯ সালের মহেশখালী ভূমিকম্প
বাংলাদেশে বিংশ শতাব্দীর শেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকম্পটি ঘটেছিল ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে মহেশখালী উপজেলায়। এর উপকেন্দ্র ছিল দ্বীপটিতে এবং ৫.২ মাত্রার এই কম্পনে বহু ঘরবাড়ির ক্ষতি হয়।
ভবিষ্যতের শঙ্কা
ভূতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, বাংলাদেশ ভারতীয়, ইউরেশীয় এবং বার্মা তিনটি টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থিত। শিলং মালভূমি, ডাউকি ফল্ট এবং মধুপুর ফল্টের মতো সক্রিয় চ্যুতিরেখাগুলো এটিকে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত করেছে। এই তিনটি প্লেটই সক্রিয়। প্রতিনিয়ত এখানে ছোট ছোট ভূমিকম্প হচ্ছে। প্লেট বাউন্ডারির পাশে বড় ধরনের ভূমিকম্পের আশঙ্কা থাকে। বিশেষজ্ঞরা বারবার সতর্ক করছেন যে, এই অঞ্চলে ১০০-১৫০ বছরের ব্যবধানে বড় মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানার ইতিহাস রয়েছে।
তবে ভূমিকম্প সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়া যায় না কখনোই, আমরা আশা করতে পারি যেন এর চেয়ে বড় ভূমিকম্প আমাদের না দেখতে হয়। এবং ভূমিকম্প হলে ভয় না পেয়ে করণীয়গুলো করতে হবে। জাপান বা ক্যালিফোর্নিয়ার মতো ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলগুলোতে ব্যাপক জনসচেতনতা, জরুরি মহড়া এবং কার্যকর দুর্যোগ মোকাবিলা ব্যবস্থা থাকলেও বাংলাদেশে এর ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে, এটি জোরদার করতে হবে। এবং ভবিষ্যৎ বিপর্যয় এড়াতে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের দ্রুত মূল্যায়ন ও সংস্কার এবং নতুন ভবন নির্মাণে কঠোরভাবে বিল্ডিং কোড মেনে চলার কোনো বিকল্প নেই।
tahmira48@gmail.com

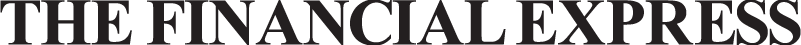
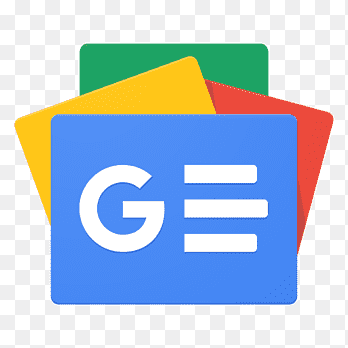 For all latest news, follow The Financial Express Google News channel.
For all latest news, follow The Financial Express Google News channel.